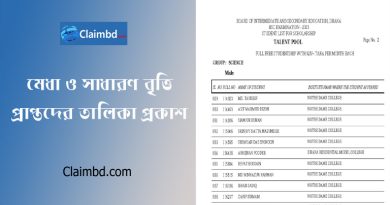৮ম পে স্কেলের পরেও মূল্যস্ফীতি হ্রাস ২০২৫ । সিপিডি’র সুপারিশ কেন একঘেয়ে?
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৮ম পে স্কেল কার্যকর হওয়ার পরও দেশে মূল্যস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি, বরং কমে এসেছে—এমন তথ্য উঠে এসেছে বার চার্ট বিশ্লেষণ করে। এই তথ্য সত্ত্বেও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর পক্ষ থেকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রায়শই বাজার নিয়ন্ত্রণ, মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ এবং মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতির সমন্বিত ব্যবহারের মতো গতানুগতিক সুপারিশগুলোই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে, যা নিয়ে অর্থনীতি বিশ্লেষকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে।
বার চার্টে মূল্যস্ফীতির প্রবণতা
চার্ট অনুসারে, গত ছয় অর্থ-বছরে মূল্যস্ফীতির হার নিম্নরূপ:
দেখা যাচ্ছে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে (যে সময়ে পে স্কেল কার্যকর হয়) মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬.১%, যা এর পূর্ববর্তী অর্থ বছর ২০১৪-১৫ এর ৬.৪% এবং ২০১৩-১৪ এর ৭.৪% থেকে কম। পে স্কেল কার্যকর হওয়ার পরে মূল্যস্ফীতি বাড়ার যে আশঙ্কা ছিল, বার চার্টের তথ্য তা সমর্থন করে না। বরং, পরবর্তী বছরগুলোতেও হার মূলত নিম্নমুখী এবং স্থিতিশীল ছিল। এটি প্রমাণ করে, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি সরাসরি মূল্যস্ফীতি বাড়ায়নি, যা সাধারণত অর্থনৈতিক তত্ত্বে একটি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।
সিপিডি’র সুপারিশ বনাম বার চার্টের তথ্য
চার্টের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮ম পে স্কেল কার্যকর হওয়ার পরও মূল্যস্ফীতি বাড়েনি। ফলে, পে স্কেলের কারণে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে—সিপিডি’র পক্ষ থেকে যদি এমন কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়, তবে তা এই তথ্যচিত্রের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।
সিপিডি’র পরামর্শগুলোর মধ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণ, মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ এবং মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতির সমন্বিত ব্যবহারের কথা বলা হয়। তবে, যেহেতু পে স্কেল কার্যকর হওয়ার পর মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ছিল এবং হ্রাসের প্রবণতা দেখা গেছে, সেহেতু অর্থনীতি বিশ্লেষকদের একাংশ প্রশ্ন তুলছেন যে সিপিডি কেন এখনও একই ধরনের সুপারিশগুলো বারবার তুলে ধরছে।
অর্থনীতিবিদদের প্রশ্ন:
- পে স্কেল কার্যকর হওয়ার পরেও যখন মূল্যস্ফীতি বাড়েনি, তখন কি সিপিডি এই সংক্রান্ত বিশ্লেষণ থেকে দূরে থেকে অন্যান্য মূল অর্থনৈতিক সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করতে পারত না?
- সিপিডি’র মতো একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান কি বাজারের কাঠামোগত দুর্বলতা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রভাবের মতো আরও গভীর ও জটিল বিষয়গুলো নিয়ে নতুন ও কার্যকর সমাধান দিতে পারে না?
- শুধুমাত্র বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপের মতো বহুল-আলোচিত ইস্যুগুলিতে জোর না দিয়ে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাপ, টাকার অবমূল্যায়ন, কিংবা আমদানি-নির্ভরতার মতো বর্তমান অর্থনীতির তীব্র সমস্যাগুলোর জন্য আরও সুনির্দিষ্ট ও সময়োপযোগী সুপারিশ করা জরুরি নয় কি?
পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, সিপিডি’র উচিত চলমান অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি অনুসারে তাদের সুপারিশমালায় বৈচিত্র্য আনা এবং একঘেয়ে বক্তব্য পরিহার করে নীতিনির্ধারকদের জন্য আরও কার্যকরী দিকনির্দেশনা প্রদান করা।
নতুন পে-স্কেল ঘোষণা হলেই দেশের অর্থনীতিবিদ ও মিডিয়ার একটি অংশ ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির (Inflationary Pressure) আশঙ্কায় সরব হয়ে ওঠে। তাদের মূল যুক্তি হলো, সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়লে বাজারে টাকার প্রবাহ বাড়বে এবং এর ফলে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে সাধারণ জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। কিন্তু এই বিতর্কের ভিড়ে দুটি মৌলিক বিষয় প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়: নিম্ন গ্রেডের কর্মীদের মানবেতর জীবনযাত্রা এবং উচ্চ গ্রেডের বেতন-বৈষম্যের আসল মুদ্রাস্ফীতি-জনক প্রভাব।
১. ৮,২৫০ টাকায় জীবনধারণের চ্যালেঞ্জ: কোথায় মিডিয়ার মনোযোগ?
কর্মকর্তাদের নতুন পে-স্কেল নিয়ে আলোচনা শুরু হলেই তা মূলত উচ্চপদস্থদের বেতন বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। কিন্তু দেশের বিপুল সংখ্যক সরকারি কর্মচারী, যাদের প্রাথমিক বেতন এখনো ৮,২৫০ টাকা বা তার কাছাকাছি, তাদের জীবনধারণের চ্যালেঞ্জগুলো আড়ালে পড়ে যায়।
- অসম প্রতিযোগিতার শিকার: ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো শহরে শুধুমাত্র ৮,২৫০ টাকা বা সামান্য বেশি বেতন দিয়ে একজন কর্মচারী কীভাবে বাসা ভাড়া, খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা খরচ মেটাবেন, তা নিয়ে কোনো বাস্তব আলোচনা হয় না। অথচ এই কর্মীরাও প্রথম গ্রেডের উচ্চ-বেতনভোগী কর্মকর্তার মতোই একই বাজার থেকে নিত্যপণ্য কিনতে বাধ্য হন, যেখানে উচ্চ বেতনধারীরা তাদের ক্রয়ক্ষমতা দিয়ে পণ্যের দাম বাড়াতে পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেন।
- বাস্তবতার নিরিখে মূল্যস্ফীতি: যদি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাই মূল লক্ষ্য হয়, তবে সরকারের উচিত সবার আগে নিশ্চিত করা যে সর্বনিম্ন বেতনভোগী কর্মীরা যেন ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারেন। তাদের সামান্য বেতন বৃদ্ধি কখনোই বাজারে উচ্চ-পদস্থদের বেতন বৃদ্ধির মতো ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে না।
২. বেতন-বৈষম্য: আসল মূল্যস্ফীতি ও সামাজিক চাপ
পে-স্কেলের কাঠামোগত বৈষম্যই আসল বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা উচিত। প্রথম গ্রেড থেকে শুরু করে শেষ গ্রেডের বেতনের পার্থক্য ৭০ হাজার টাকা বা তার বেশি হতে পারে। এই বিপুল ব্যবধান বাজার অর্থনীতিতে গুরুতর প্রভাব ফেলে:
- উচ্চ ক্রয়ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ: প্রথম গ্রেডের হাতে থাকা অতিরিক্ত অর্থ বাজারে বিলাসবহুল পণ্য এবং বিশেষ সেবার চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। এই কেন্দ্রীভূত উচ্চ ক্রয়ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট স্তরে “ডিমান্ড-পুল” মূল্যস্ফীতি তৈরি করে, যা মূলত সুবিধাভোগীদের জীবনযাত্রাকে আরও উন্নত করে, কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য নিত্যপণ্যের বাজারকে আরও কঠিন করে তোলে।
- নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন: একই দেশ, একই বাজার থেকে পণ্য কেনা সত্ত্বেও বেতনের এই আকাশ-পাতাল পার্থক্য সমাজে একটি তীব্র অসন্তোষ ও বৈষম্য তৈরি করে। এই বৈষম্য দূর করার আলোচনা না করে শুধুমাত্র নিম্ন গ্রেডের কর্মীদের সামান্য বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব এলেই মুদ্রাস্ফীতির জুজু দেখানোটা যুক্তিসঙ্গত নয়।
৩. পে-স্কেল সংস্কারের যৌক্তিক প্রস্তাব: ১:৪ অনুপাতে বেতন সমন্বয়
যদি সত্যিই নতুন পে-স্কেল মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে দেয়, তবে এর সমাধান কর্মীদের বেতন কমানো নয়, বরং উচ্চ-পদস্থদের অতিরিক্ত বেতন-বিলাসিতা নিয়ন্ত্রণ করা।
আপনার প্রস্তাবিত ১:৪ অনুপাতে বেতন সমন্বয়ের যুক্তিটি অত্যন্ত শক্তিশালী। অর্থাৎ, যদি সর্বনিম্ন গ্রেডের বেতন হয় , তবে সর্বোচ্চ গ্রেডের বেতন -এর বেশি হওয়া উচিত নয়।
- সাংবাদিকদের বেতন কাঠামোর প্রসঙ্গ: আপনি সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, যে মিডিয়া হাউসগুলো মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ে সরব, তাদের নিজস্ব কর্মীদের (সাংবাদিক ও অন্যান্য) বেতন কাঠামোতে প্রায়শই অসামঞ্জস্য দেখা যায়। তাদেরও উচিত প্রথমে নিজেদের কর্মীদের জীবনধারণের মতো বেতন নিশ্চিত করা। যদি তারা থেকে শুরু করে একটি পে-স্কেল চালু করে দেখেন যে সেই বেতনে জীবনধারণ সম্ভব কি না, তবেই তারা নিম্ন গ্রেডের কর্মচারীদের বাস্তব জীবন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতে পারবেন।
অতএব, নতুন পে-স্কেল নিয়ে আলোচনা শুরু হলে তার ফোকাস হওয়া উচিত কাঠামোগত বেতন-বৈষম্য দূর করা এবং সর্বনিম্ন আয়ের কর্মীদের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা। শুধুমাত্র মুদ্রাস্ফীতির একঘেয়ে ভয় না দেখিয়ে, অর্থনৈতিক আলোচনাকে উচ্চ-পদস্থদের লাগামহীন বেতন এবং এর ফলে বাজারে সৃষ্ট অসম প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত।